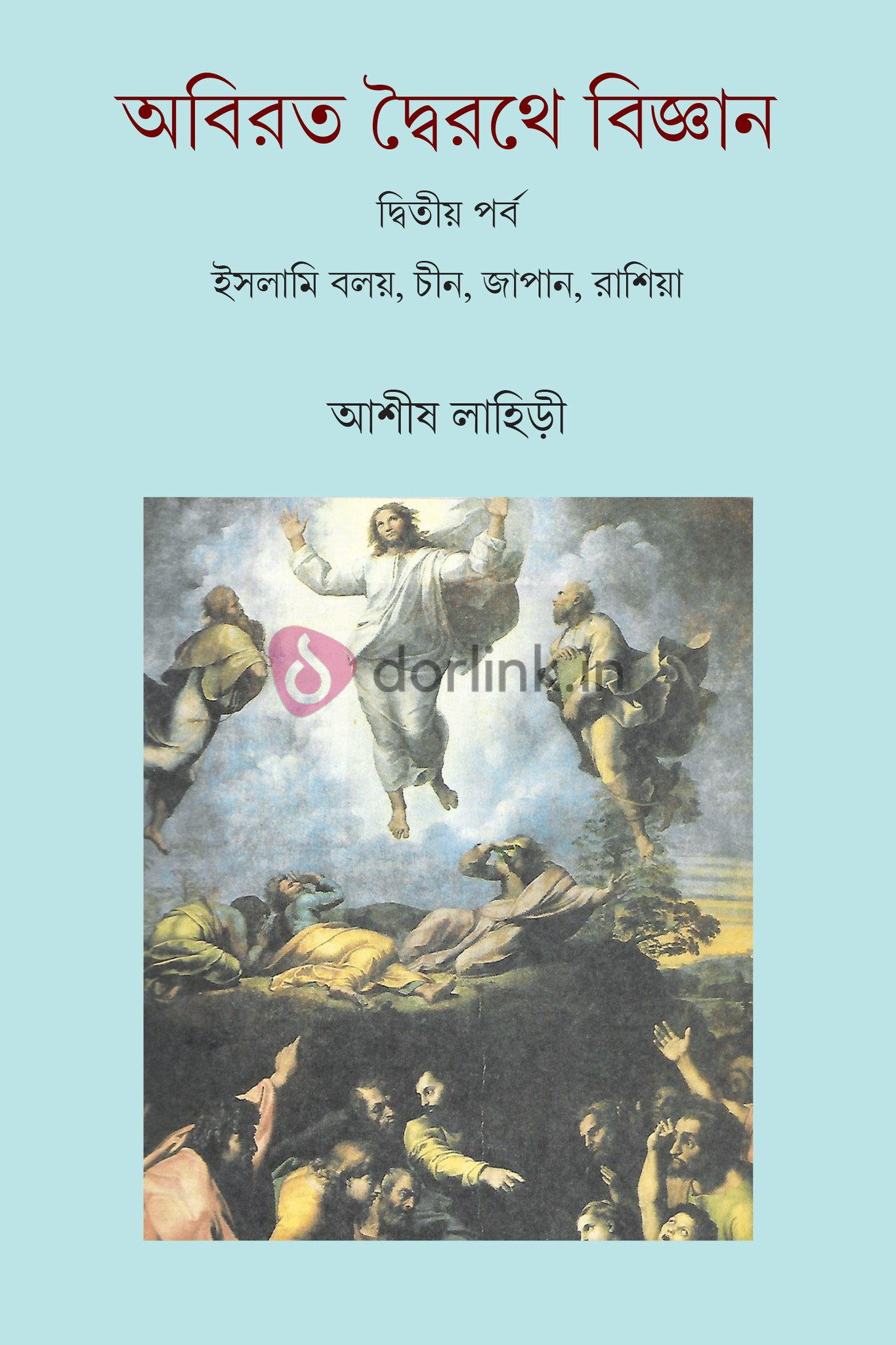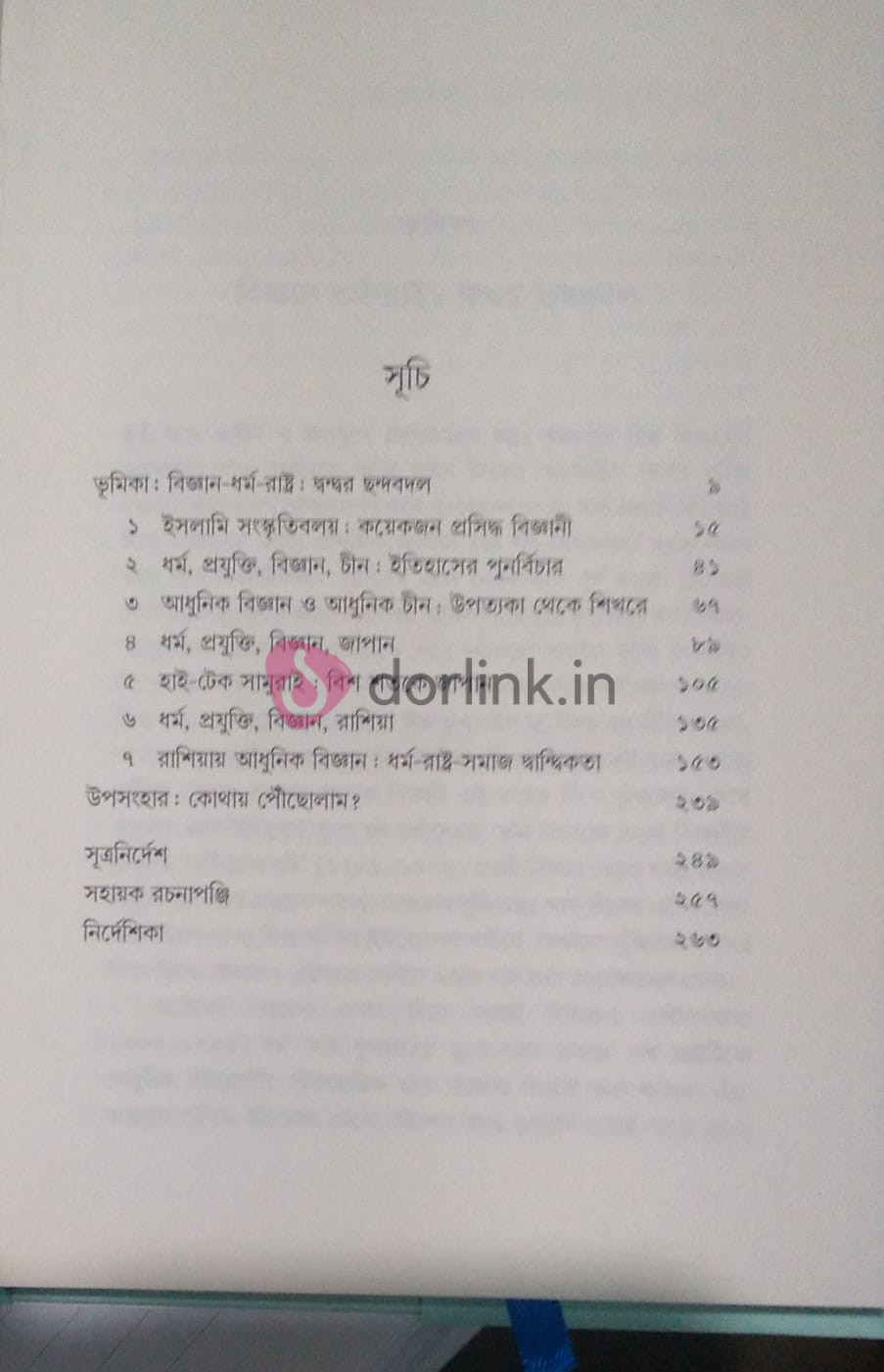Writer : Ashis Lahiri
- Shipping Time : 10 Days
- Policy : Return/Cancellation?
You can return physically damaged products or wrong items delivered within 24 hours with photo/video proof.
Contact Customer Support for return initiation and receive return authorization via email. Securely package for return.
Refunds for eligible returns are processed within 7-10 business days via Bank Transfer.
Order cancellation allowed within 24 hours of placing it. Standard policy not applicable for undamaged/wrong product cases. Detailed info. - Genre : Essays>Social/Educational/Economic Criticism
- Publication Year : 2023
- ISBN No : 978-81-95974-37-5
- Binding : Paste Board (Hard) with Gel Jacket
- Pages : 272
- Weight : 515 gms
- Height x Width x Depth : 8.5x5.5x01 Inch
If so, it will be notified
About the Book
ধর্ম ও বিজ্ঞানের সংঘাত মানবসভ্যতার ইতিহাসে এক চিরন্তন অধ্যায়। একদিকে বিশ্বাস, অলৌকিকতা ও ঐশী অনুপ্রেরণার জগৎ; অন্যদিকে যুক্তি, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষানির্ভর সত্যের অন্বেষণ—এই দুই ধারার টানাপোড়েনই সভ্যতার বৌদ্ধিক অগ্রযাত্রাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। আশীষ লাহিড়ীর ‘অবিরত দ্বৈরথে বিজ্ঞান’ এই দীর্ঘ ও জটিল সংঘাতের ইতিহাসকে দুই খণ্ডে বিশ্লেষণ করেছেন অনন্য দক্ষতায়।
হিন্দু-বৌদ্ধ ভারতের প্রাচীন পরিমণ্ডলে যেখানে বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক ছিল গুপ্ত ও দার্শনিক, সেখানে খ্রিস্টীয় ও ইসলামি কৃষ্টি-বলয়ে সেই সংঘাত রূপ নেয় এক তীব্র ও প্রকাশ্য দ্বন্দ্বে। রাশিয়ার ইতিহাসে দেখা যায় রাষ্ট্র ও বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ মিথষ্ক্রিয়া, আর চীনে ও জাপানে সমাজ ও রাষ্ট্রের নানা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই দ্বৈরথের রূপ পাল্টেছে বহুবার। আধুনিক যুগে যখন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি রাষ্ট্রশক্তির মূল ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত, তখন লেখক এক গভীর প্রশ্ন উত্থাপন করেন—আজ কি রাষ্ট্রই ধর্মের জায়গা নিয়েছে? রাশিয়া, আমেরিকা, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের ইতিহাস কি সেই দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করছে?
দ্বিতীয় খণ্ডে আশীষ লাহিড়ী বিশেষভাবে মনোনিবেশ করেছেন বিংশ শতাব্দীর সূচনায় বিজ্ঞান ও রাষ্ট্রচিন্তার পারস্পরিক সম্পর্কের দিকে। রুশ মনোবিজ্ঞানী ইভান পাভলভ এবং বিপ্লবী গণিতবেত্তা সোফিয়া কোভালেভস্কায়াকে ঘিরে তাঁর বিশ্লেষণ পাঠককে নিয়ে যায় সেই সময়ের সামাজিক ও বৌদ্ধিক অস্থিরতার কেন্দ্রে। পাশাপাশি তিনি আলোচনা করেছেন জাপানে বস্তুবাদী ও ভাববাদী বিজ্ঞানীদের বিতর্ক, চীনের বৈজ্ঞানিক অভিযাত্রার সংক্ষিপ্ত কিন্তু গভীর ইতিহাস, এবং ইসলামী ও খ্রিষ্টীয় বলয়ের মধ্যে বিজ্ঞানচর্চার উত্থান-পতনের ধারাবাহিকতা।
পাঠক অমিত বেরা, যিনি দিল্লিতে থেকে একটি হিন্দি পত্রিকায় আর্থিক ও সামাজিক বিষয়ে লেখেন, নিজের প্রতিক্রিয়ায় লিখেছেন যে, বাংলায় বিজ্ঞানের ইতিহাস নিয়ে এত সহজপাঠ্য অথচ গভীর ভাবনাসমৃদ্ধ বই তিনি খুব কম পড়েছেন। তাঁর মতে, সোফিয়া কোভালেভস্কায়া ও পাভলভ সংক্রান্ত অধ্যায়গুলি বইটির সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ। বিশেষভাবে তিনি উল্লেখ করেছেন লেখকের ঐতিহাসিক ও দার্শনিক বিশ্লেষণের গভীরতা, যা বাংলায় বিরল।
তবে পাঠকের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণও রয়েছে — ১৯৩১ সালে লন্ডনে আয়োজিত বিশ্ব দর্শন সম্মেলনে সোভিয়েত বিজ্ঞানী বরিস হেসেনের বিখ্যাত প্রবন্ধ “The Social and Economic Roots of Newton’s Principia” সম্পর্কে বইটিতে কোনো আলোচনা নেই। অথচ বিজ্ঞানের ইতিহাসে সেই প্রবন্ধটি মার্কসবাদী বিজ্ঞানচর্চার অন্যতম মাইলফলক। ১৯৩৬ সালে হেসেনকে ‘সমঝোতাবিরোধী কার্যকলাপ’-এর অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, আর তাঁর বন্ধু ইগোর ট্যাম পরে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। এই অনুপস্থিতি পাঠকের মনে সামান্য অতৃপ্তি রেখে যায়, কিন্তু তাতে বইটির বিশ্লেষণাত্মক গুণ কমে না।
ভারতে বিজ্ঞানের ইতিহাস ও দর্শন নিয়ে গবেষণার ধারাটি দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের পর ক্রমে নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল। সেই জায়গায় আশীষ লাহিড়ী তাঁর লেখনিতে সেই প্রবাহকে নতুন প্রাণ দিয়েছেন। রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, মীরা নন্দা এবং ধ্রুব রায়নার মতো চিন্তকের সঙ্গে তিনি বাংলায় বিজ্ঞানের সমাজদর্শন চর্চাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন আরও বিস্তৃত পরিসরে।
‘অবিরত দ্বৈরথে বিজ্ঞান’ কেবল ধর্ম ও বিজ্ঞানের সংঘাতের ইতিহাস নয়; এটি এক চিন্তাপ্রবণ যাত্রা—যেখানে রাষ্ট্র, সমাজ ও মানুষের মুক্তচেতনার বিবর্তন একসূত্রে গাঁথা। আধুনিক বিজ্ঞানের জন্ম থেকে শুরু করে রাষ্ট্রশক্তির প্রভাবে তার রূপান্তর পর্যন্ত, আশীষ লাহিড়ীর বিশ্লেষণ পাঠককে বাধ্য করে ভাবতে—বিজ্ঞান কি সত্যিই মুক্ত? আর রাষ্ট্র কি আজ নতুন ধর্ম হয়ে উঠছে?
এই বই তাই শুধু ইতিহাস নয়, এক গভীর দার্শনিক অনুসন্ধান—যেখানে ‘অবিরত দ্বৈরথে’ ধরা আছে মানবসভ্যতার চিন্তার গতিপথ।